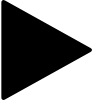গণসংগীত রচনা করার হাতে খড়ি আমার হয়েছিল গণনাট্য সংঘ গড়ে ওঠার বেশ কিছু আগে থেকেই। আমি থাকতুম আমার মামার বাড়ি সোনারপুর থানার অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রামে (এখন নাম সুভাষগ্রাম)। ওখান থেকে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে বঙ্গবাসী কলেজে পড়তে যেতুম। সোনারপুর অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন তখন বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। বিদ্যাধরী নদী মজে যাওয়ায় বঙ্গোপসাগরের নোনা জল ঢুকে হাজার হাজার বিঘে ধান জমি নোনাজলে ভেসে গিয়ে অনাবাদী হয়ে গিয়েছিল। ফলে লক্ষ লক্ষ কৃষক ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়েছিল। সেটা ব্রিটিশ আমল। দাবি ছিল ড্রেজার দিয়ে খাল কাটতে হবে। মজা বিদ্যাধরীর বালু তুলে ফেলে দিয়ে ওটাকে জীবন্ত করে তুলতে হবে। তাছাড়া কৃষককে ভরতুকি দিয়ে স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে চাল, আটা, ডাল, শিশুদের জন্য দুধ আর রোগীর জন্য ওষুধ বিতরণ করতে হবে। পিপলস রিলিফ কমিটির একটা শাখা গড়ে উঠেছিল আমাদের গ্রামে। তারা দুধ-ওষুধ বিনামূল্যে চাষীদের মধ্যে বিতরণ করতো। আমি কখন অজান্তে এই কৃষক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লুম। স্থানীয় দু’একজন কৃষক নেতা আমার কাছে একদিন এলেন এই আবদার নিয়ে যে আসন্ন কৃষক সম্মেলনের জন্য দু’একটি গান রচনা করে আমায় গাইতে হবে। কলেজে আমি তখন বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির সংশ্রবে এসেছি (১৯৪১-৪২ সালের কথা)। ছাত্র ফেডারেশনও করি অল্পস্বল্প। আবার অন্যদিকে বাঁশি বাজিয়ে হিসেবেও খুব নাম আমার। গ্রামেই শুধু নয়, কলেজেও ইন্টার কলেজ কমপিটিশনে পরপর তিনবার বাঁশিতে এস্রাজে প্রথম হয়েছি। তিমিরবরণের অর্কেষ্টাতেও ঢুকেছি। কিন্তু গানবাজনা যদিও ছোটবেলা থেকেই শিখেছি সেটা ছিল অন্য ব্যাপার। তাকে টেনে এনে আন্দোলনের কাজে লাগানোর কথা কোনদিন মনে আসেনি। কৃষক নেতারা বল্লেন – ‘লক্ষাধিক মানুষের সমাবেশ হবে — মাইক থাকবে, সেখানে তুমি গান গাইবে — সেটা হবে একটা অন্য ব্যাপার।’ শুনে আমার বুক ঢিপ্ঢিপ্ করতে লাগল – বল্লুম: “কিন্তু ওরকম গান তো আমি কোনদিন বাঁধিনি বা গাইনি!” —ওঁরা প্রচন্ড উৎসাহ দিয়ে চলে গেলেন ‘তুমি একটু চেষ্টা করলেই পারবে।’ – তখন আমি একটা ডান্সপার্টিতে ঢুকেছি। মিউজিক ডায়রেকটর সুশান্ত ব্যানার্জী, তিমিরবরণের অ্যাসিস্ট্যান্ট! রোজ কলেজের পর রিহার্শাল করতে যাই—রাত করে বাড়ি ফিরি। ভুলেই গেলুম কৃষক সম্মেলনের কথা। তারপর একদিন ওঁরা এসে হাজির— ‘চলো’! ‘কোথায়’? জিজ্ঞাসা করলুম। ‘সন্দেশখালি’ ওরা বললেন ‘কালকেই সম্মেলন। গান রেডি তো?’— কী সব্বোনাশ! বল্লুম- না না গান রেডি নেই, আর ওসব গান আমার দ্বারা হবে না – আমি যাব না’ ওরা নাছোড়বান্দা ‘ঠিক আছে গান গাইতে হবে না, এমনি চলো।’ শ্যামবাজার থেকে একটা লঞ্চে চেপে যাত্রা শুরু হল। যেতে যেতে ওরা বল্লেন- ‘তোমার নাম প্রচার হয়ে গেছে – তুমি গাইবেনা?’ – আমার একটা সিঙ্গল রীডের ছোট হারমোনিয়ম ছিল— বাবা কিনে দিয়েছিলেন। সেটা ওরা তুলে নিয়ে এসেছিলেন সঙ্গে। ভাবলুম চাষাভুষোর জন্যে গান, কী আর এমন শক্ত ব্যাপার। একটা সাদামাটা সুর করে কথা বসিয়ে গেয়ে দিলেই হবে। কিন্তু সাদামাটা সুর করাটা কতো শক্ত! শেষ পর্যন্ত ভাটিয়ালী সুর ভিত্তি করে একটা গান বেঁধে সম্মেলনে গাইলুম — (গানটা এখনও মনে আছে)
‘দেশ ভেসেছে বানের জলে
ধান গিয়েছে মরে
কেমনে বলিব বন্ধু গ্রামের কথা তোরে।’
প্রচণ্ড হৈচৈ সাড়া পড়ে গেল। দুবার তিনবার করে গাইতে হল। তখন আমার বড়জোর আঠারো কী উনিশ বছর বয়স হবে। রক্তে আগুন লেগে গেল। এর আগে বহু ছোটখাটো জলসায় তখনকার দিনের সিনেমার হিট্ পঙ্কজ মল্লিকের গান রেকর্ডে মৃণালকান্তি ঘোষ, ধীরেন দাসের গান গেয়ে বেশ কিছু আসর মাতিয়েছি। তিমিরবরণের অর্কেষ্টায় ফেলু নায়ার, শীলা হালদারের মতো নর্তক নর্তকীর সঙ্গে বাঁশি বাজিয়ে বাহবা কুড়িয়েছি। কিন্তু এমন সম্বর্ধনা, এমন করে মানুষের ভালোবাসা পাওয়া ছিল আমার স্বপ্নের অতীত। সেই যে শুরু হল তারপর আর আমার ছাড় নেই। কৃষকদের নানান দাবি দাওয়া জমিদারের জোতদারের শোষণ ‘লাঙ্গল যার জমি তার’- আন্দোলন এই সব নিয়ে গান রচনা শুরু হল। কেননা প্রায় প্রত্যেক ছোটবড়ো মিটিংয়ে আমার ডাক পড়ত। ততদিনে ছেলেদের নিয়ে একটা গানের দলও গড়ে উঠেছে। আমরা গোটা চব্বিশ পরগণা গান গেয়ে চষে বেড়াতে লাগলুম। ফলে বি.এ.তে ইংরেজী অনার্স নিয়েছিলুম সেটা ছাড়তে হল। কলেজে পার্সেন্টেজ এমন কম হল যে প্রিন্সিপ্যাল প্রশান্ত বসু একদিন ডেকে পাঠিয়ে বললেন— ‘তোমায় তো পরীক্ষায় বসতে দেয়া হবে না।’ – ইকনমিক্সেই আমার সব চেয়ে কম হাজিরা ছিল- অধ্যাপক করুণা বাবু একবার একটা পিকনিকে অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে আমাদের গ্রামের বাড়িতে এলেন। সারাদিন ধরে বাঁশি বাজালুম আর কৃষক আন্দোলনের গান শোনালুম। করুণাবাবু ছাত্রদের সামনে ঘোষণা: করলেন ‘সলিলের পার্সেন্টেজ পাওনা পুরো হয়ে গেছে, আমি প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলবো।’ ওই সব কৃষকদের জন্য রচিত গানের বেশীর ভাগই গেছে হারিয়ে! এমনিতেই আমি চিরকেলে বাউণ্ডুলে। আণ্ডার গ্রাউন্ডে থাকাকালীন গানের খাতা কোথায় যে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল সে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমনি করে আমার দুটো নাটক ‘জনান্তিকে’ আর ‘সংকেত’ এর পাণ্ডুলিপিও চিরকালের জন্য লুপ্ত হয়ে গেছে স্বাধীনতার পর যখন পার্টি বে-আইনী হল সেই সময় আণ্ডারগ্রাউন্ডে থাকাকালীন। আমার গানগুলোর মতো দুটি নাটকও ‘নিষিদ্ধ’ ঘোষিত হয়েছিল। সে কথা থাক। প্রাক স্বাধীনতা যুগে ফেরা যাক। বোধহয় ১৯৪৫ সালে অবিভক্ত বাংলায় রংপুরে ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তখন বন্দীমুক্তি আন্দোলন জোরদার। ‘চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে’র বন্দীদের আন্দামান থেকে ফেরত এনে তাদের আবার বিচারের কথা ঘোষণা করেছিল ব্রিটিশ সরকার। তাছাড়া বোধহয় আই এন এর যুদ্ধবন্দীদের লালকেল্লায় বিচারের কথাও ঘোষিত হয়েছিল। ওই রংপুর ছাত্র সম্মেলনে ‘বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা’ গানটি রচনা করে আমি গাই। সম্মেলন চলাকালীন অন্তত দশবার আমায় গানটি গাইতে হয়েছিল। গণনাট্য সংঘ যদিও গঠিত হয়েছিল, আমি তখনও তাতে যোগ দিইনি। ওই গানটির পিছনে একটু ছোট্ট ইতিহাস আছে যেকথা বলি। বাংলার কীর্ত্তনাঙ্গ গান মূলত প্রেমরসের ভক্তিরসের গান- ‘ওই অঙ্গে কোন বলিষ্ট গান রচনা সম্ভব নয়’ একথা প্রায় শুনতাম পেশাদার কিছু সুরকারদের মুখে। আমি গানটি রচনা করেছিলাম ‘যমুনে তুমি কি সেই যমুনে প্রবাহিনী’ সুরটিকে ভেঙ্গে। শুনেছি বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের সময় শয়ে শয়ে ছেলেমেয়ে ওই গানটি গাইতে গাইতে মিছিলে শামিল হতেন। বলিষ্ট প্রতিবাদের এরচেয়ে বড়ো নজির আর কি হতে পারে? আসামের ‘বিহু’ গানের সুরও মূলত আনন্দোচ্ছল প্রেমরসাত্মক নৃত্যের সহযোগী সংগীত। ওই সুরকে ভিত্তি করে আমি সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গান রচনা করি— ‘ও মোদের দেশবাসীরে/ আয়রে পরান ভাই আয়রে রহিম ভাই/ কালো নদী কে হবি পার’— গানটি। ওই একই সুরে ফুটে ওঠে একটি উদ্দীপ্ত আহ্বান। আবার একই সুরে বিষাদের ছায়া নেমে আসে ‘গাঁয়ের বধু’ গানের শেষ চরণে— ‘আজও যদি তুমি/ কোন গাঁয়ে দেখ ভাঙ্গা কুটীরের সারি’—। সুরকার হিসাবে আমার শিক্ষা এই যে প্রয়োগ-পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে একটি সুর শ্রোতাদের মনে কোন রস উৎপাদন করবে। নিগ্রো স্পিরিচুয়াল গানের বেদনা ভরা হতাশার সুরে বাঁধা পল রোবসনের কণ্ঠে ‘ওল্ড ম্যান রিভার’ একটা উত্তরণ ঘটায় আবার প্রায় ওই একই সুরে ভূপেন হাজারিকার ‘গঙ্গা তুমি বইছ কেন?’ অন্যতর এক আকুতি জাগায়। যা বলছিলাম— ওই ‘বিচারপতি’ গানের তুমুল অভ্যর্থনা আমার জীবনের একরকম মোড় ফিরিয়ে দিল। আমি নাচের পার্টিতে বাঁশি বাজানো ছেড়ে দিলাম। যদিও তখনকার দিনে একটা নাচের অনুষ্ঠানে বাঁশি বাজালে আমি পেতাম ৫০ টাকা যা আজকালকার মূল্যে দু’হাজার টাকার মত হবে। কিন্তু ওতে আমার মন বসলো না। এখানে বলে রাখি যে দুজন কমরেড আমায় কৃষকদের জন্যে গান লেখায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁরা হলেন: কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কৃষক নেতা কর্মী খেপুদা বা খগেন রায়চৌধুরী আর হরিধন চক্রবর্তী যাকে টেকনামে ‘জীবন’ বলে সবাই জানতেন (এঁরা দুজনেই আজ প্রয়াত)। আর একজন হলেন কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরী। উনি ছিলেন ২৪ পরগনা জেলার পার্টি সম্পাদক। উনি আমায় বলেছিলেন ‘সলিল তুমি শুধু গান লিখে যাও – যা মনে আসবে তাই নিয়ে গান লেখো, সুর করো।’ ওই সময় আমি লিখেছিলুম একটি ব্যক্তিগত গান যা অনেক বছর পরে উৎপলা সেনের কণ্ঠে রেকর্ড হয়েছিল— গানটি হল : ‘প্রান্তরের গান আমার/ মেঠো সুরের গান আমার/ হারিয়ে গেল কোন বেলায়। আকাশে আগুন জ্বালায় / মেঘলা দিনের স্বপন আমার ফসলবিহীন মন কাদায়।’ এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তের কথা। বলে পাঠালেন আমার গানের একটা ক্যাসেট ওঁকে দিতে, চীনে গিয়ে অবসর সময়ে শুনবেন বলে। আমি আমার যত গণসংগীত একটা ক্যাসেটে ভরে ওঁকে দিয়ে এলাম। দুদিন পরে বুদ্ধদেব (ভট্টাচার্য) আমায় বললেন— গণসংগীত নয়, উনি রচিত সব আধুনিক গানও শুনতে চান। ‘গায়ের বধূ’, ‘রানার’, ‘পালকী চলে’, ‘সাত ভাই চম্পা’ ইত্যাদি। বলতে দ্বিধা নেই আমি কিছুটা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম ওই রকম গুরুগম্ভীর পার্টির নেতা আধুনিক গান শুনতে চান। আমি হেমন্ত, লতা, দ্বিজেন ইত্যাদির গাওয়া গান যা তাড়াতাড়িতে হাতের কাছে পাওয়া যায় ক্যাসেট ভরে আবার ওঁকে দিয়ে এলাম। বুদ্ধর মুখে শুনেছি উনি চীনে গিয়ে ক্যাসেটটি বোধহয় মিনিষ্ট্রী অব কালচারের কোন নেতার হাতে দেন। তারপর যখন চীনা গান শুনে শুনে অতিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন, শরীরও তখন অসুস্থ, ওই ক্যাসেটটি ফেরৎ চেয়ে পাঠান। কিন্তু হা হতোস্মি! সে ক্যাসেট তখন সংস্কৃতি দপ্তরের কোন অতলে তলিয়ে গেছে, সে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। তারপর তো মারাই গেলেন। এ দুঃখ আমার কোনদিন যাবে না যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে আমার গান প্রমোদদা শুনতে চেয়েও শুনতে পাননি! – আবার আগের কথায় ফিরি— ১৯৪৬-এর সারা ভারত ব্যাপী রেল ধর্মঘটের প্রাক্কালে তার প্রস্তুতিপর্বে কমরেড বীরেশ মিশ্র আমায় ডেকে পাঠালেন। গোটা উত্তরবঙ্গ থেকে সারা আসাম উনি পরিক্রমা করবেন বিভিন্ন স্টেশনে রেলশ্রমিকদের মিটিং করে করে। আমাকে সঙ্গী হতে বললেন প্রত্যেক মিটিং-এ হতে আমায় গাইতে হবে। একটা ইঞ্চিনের বগীতে চেপে শুরু হল বীরেশদার সঙ্গে আমার যাত্রা। সাথী শুধু আমার সেই সিঙ্গেল রিডের হারমোনিয়ম। রেলশ্রমিকদের নানারকম সমস্যা, দাবিদাওয়া ইত্যাদি নিয়ে বিশদ আলোচনা করতেন আর আমি গান লিখতাম, গাইতাম প্রত্যেক মিটিংয়ে। সেসবও কোথায় লুপ্ত হয়ে গেছে। বেঁচে আছে শুধু একটি গান। চলন্ত রেলগাড়ীর চাকার শব্দের ছন্দে রচিত ‘ঢেউ উঠছে/ কারা টুটছে/ আলো ফুটছে/ প্রাণ জাগছে।’ ১৯৪৫ সালের ২৯শে জুলাই সারা ভারতব্যাপী ধর্মঘটের ঠিক আগের দিনে ময়দানে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসমাবেশে গানটি পাওয়া হল।
শোষণের চাকা আর ঘুরবে না ঘুরবে না
চিমনীতে কালো ধোঁয়া উঠবে না উঠবে না
বয়লার চিতা আর জ্বলবে না জ্বলবে না— . . .
আজ হরতাল/ আজ চাকা বন্ধ
‘তাৎক্ষণিক’-ফল সিদ্ধির জন্য রচিত গানগুলির কিছু কিছু বেশ ভালো ছিল। তবু সেগুলি হারিয়ে গেছে বলে আমার দুঃখ নেই। বলতে পারি ওগুলো ছিল আমার ‘অনুশীলন’ পর্ব— কতরকম সুর ছন্দ ভাব নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতাম— খেপুদা হরিধনও যেমন বলেন নি বীরেশ দাও ভালোমন্দ কোন কথা বলতেন না। মাঝে মাঝে শুধু বলতেন- ‘এবার একটা সহজ সুরে ভালো গান লেখ’- কিন্তু আমার মন মানবে কেন? বিলিতি বহু সিম্ফনী শুনে শুনে যার মন পোক্ত হয়েছে— বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রকে রপ্ত করে পেশাদারী সংগীতপ্রসারের শিক্ষা যার হয়েছে সে তো চাইবেই প্রতি পদে চমক লাগাতে, তার ওপর তখন কাঁচা বয়স। ছোটবেলা থেকে যত গান শুনেছি শিখেছি তার কোনটার মতোই আমার গান হবে না। সে স্বতন্ত্র সত্ত্বায় নিজের পায়ে নিজে দাড়াতে পারবে এবং তার মধ্য দিয়ে উদ্দেশ্য সাধন করবে এই ছিল আমার স্বপ্ন! সেই সময় গণনাট্যের অন্যতম নেতা ভূপতি নন্দীর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে, আমি আত্মগোপন করে আছি জেনেও ওঁর বাড়িতে আমায় আশ্রয় দেন। গড়িয়াহাটের মোড়ে তখনকার দিনে বিশাল বাড়ি ‘যশোদা ভবনের’ পাঁচ তলায় ছিল সে ফ্ল্যাট। সেখানে আমি থাকতে শুরু করলুম। ও বাড়ির মা ভাই বোন সবাই কমিউনিস্ট পার্টির গোড়া সমর্থক আর ছিল গানবাজনার ভক্ত। ভূপতিদা নিজে ছিলেন সুগায়ক। গণসংগীতের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়সংগীত, রবীন্দ্রসংগীতের রীতিমত চর্চা ছিল ও বাড়িতে। ওখানে গণনাট্যের এবং রবীন্দ্রসংগীতের তাবড় তাবড় বড়ো শিল্পীদের যাতায়াত ছিল। ভূপতিদার মাধ্যমেই আমার পরিচয় হয় বিনয় রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র এবং পরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। আমি গ্রামে থাকলে যেটা কোনোদিনই সম্ভব হত না। ভূপতিদার কল্যাণে এই সব কিংবদন্তি শিল্পীস্রষ্টাদের মোহময় জগতের চাবি এক লহমায় খুলে গেল আমার কাছে। আমি গায়ের ছেলে গেঁয়ো চাষিভুসোদের জন্যে গান লিখি। আর এঁরা সব মার্জিত পরিশীলিত জগতের লোক, প্রথম প্রথম ভীষন কুণ্ঠা হত আমার। ভয় ভাঙলো বিনয়দা যখন আমার গান ‘বিচারপতি’ গেয়ে শোনালেন- কী করে জানিনা ওই গানটি ওঁদের সবার জানা হয়ে গেছে। আর এই ‘যশোদা ভবনে’র বাড়িতে বসেই ‘আলোর পথযাত্রী’ থেকে শুরু করে আমার অধিকাংশ গণসংগীত রচিত হয়েছে। গান তৈরি না হতে হতেই ভূপতিদা, সুরপতি, ভূপতিদার বোন মানী, তা ছাড়া রেবা রায়, কলিম সরাফী ইত্যাদিরা শিখে নিয়ে কোরাসে গাইতে শুরু করতেন। প্রতিদিন নতুন নতুন গান তৈরি করার তাগিদ অনুভব করতুম। ঐখানে বসেই আমি প্রথম গানে হার্মনি প্রয়োগ করে গান রচনা করলাম ‘আলোর দেশ থেকে- আঁধার পার হতে কে যেন ডাকে আমায়’- পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত দেশের ডাক যেন এসে পৌঁছেছে এমনি একটা ইশারা ছিল। গণনাট্য সংঘের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগসূত্র এইখানেই স্থাপিত হল। এইখানে থাকতেই আমি মার্কসীয় তত্ত্ব- মার্কসবাদী সাহিত্য, শিল্প, সোভিয়েত লিটারেচার নিয়ে গভীরভাবে পড়াশোনা শুরু করি। এবং আগেই খেপুদার দৌলতে আমি মার্কসবাদ নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিলাম। খেপুদা ছিলেন মার্কসীয় তত্ত্বে সুপণ্ডিত। লেনিনের লেখা One Step Forward Tow Steps Back ইত্যাদি বই থেকে মার্কসবাদের tactical প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করতে পারতেন তিনি। যশোদাভবনে ভূপতিরা নিজেরা যদিও বেশি পড়াশোনা করতেন না- বইয়ের সংগ্রহ ছিল ভালোই। ওখানেই আমি প্রথম এঙ্গেলসের Origin of Family, Private Property and State পড়ি। আমার জন্মগত সংস্কারের অধিকাংশই ভেঙে গেল ওই বইটি পড়ে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশকাল সমাজ সভ্যতাকে দেখতে শিখলাম। তারপরে পরিচয় হল ম্যাক্সিম গোর্কির সঙ্গে। My University লেখা ওঁর আত্মজীবনী পড়লুম। পড়লুম Mother— ভিন্নতর স্বাদ। নায়কের সংজ্ঞায় নতুন মাপকাঠি আমাকে মুগ্ধ করল— পাভেল আমার হিরো হয়ে গেল। ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যচর্চার ঝোঁক ছিল আমার। স্কুলে পড়াকালীনই আমি কবিতা লিখতাম রবীন্দ্রনাথকে ডাহা অনুকরণ করে, সেই প্রভাবকে কাটিয়ে উঠতে আমায় সাহায্য করেছিল পল্ এলুয়ার, পাবলো নেরুদা-র কবিতা। আমার প্রথম দিককার কিছু কিছু গানের সুরে রবীন্দ্রসংগীতের প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও যেমন ‘হাতে মোদের কে দেবে সেই ভেরী’ গানে— সেটা কাটিয়ে উঠে আমার নিজস্ব ষ্টাইল তৈরি করতে সাহায্য করেছিল একদিকে গণসংগীত নতুন আঙ্গিকের তাগিদ, অন্যদিকে পাশ্চাত্য সংগীতের সঙ্গে আমার আত্মিক যোগসূত্র। তাছাড়া আঞ্চলিক বিভিন্ন ভারতীয় লোক-সংগীতের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে গণনাট্য সংঘের বার্ষিক সম্মেলনগুলিতে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকশিল্পীরা এসে জড়ো হতেন তাদের গানের ভাণ্ডার নিয়ে। তখনকার দিনে তো আর টেপরেকর্ডার ছিল না। স্বরলিপি লিখে নিয়ে কিছুটা, আর কিছুটা সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় কথা বসিয়ে নিয়ে। এমনি করে তেলেগু একটি লোকসংগীত থেকে জন্মালো আমার ‘মানব না বন্ধনে, মানব না শৃঙ্খলে’ গানটি। গোর্কির মত আমিও বলতে পারি এই সম্মেলনগুলিই আমার Music University- স্বাধীনতার ঠিক পরেপরেই আমি লিখলাম-
‘নাকের বদলে নরুন পেলুম
—টাক ডুমাডুম ডুম
জান দিয়ে জানোয়ার পেলুম
লাগল দেশে ধূম’।
গানটি সঙ্গে সঙ্গে ব্যান হল। পরে পার্টি থেকেই গানটি গাওয়া বারণ হল। কারণ ওটা ‘ঝুটা আজাদি’র ভুল তত্ত্বের ওপর লেখা বলে। কিন্তু আমি এখনও মনে করি গানটি লেখা ঠিক হয়েছিল। স্বাধীনতা উত্তর পর্বে শিশুরাষ্ট্র রক্ষার নামে যে অত্যাচারের তাণ্ডব নেমে এল কৃষক শ্রমিক আন্দোলনের ওপর, তার কোন নজির আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্বেও বিরল। ‘তেভাগা’ আন্দোলনের সময় আমি আর শহরে বসে থাকতে পারলুম না। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় আমার কমরেডদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। তখনই লেখা হয়েছিল— ‘হেই সামালো ধান হো/ কাস্তেটা দাও শান হো/ জান কবুল আর মান কবুল/ আর দেব না আর দেব না রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো’– তারপরে অহল্যা-মা’র সঙ্গে আরও কৃষক রমণীদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে লিখেছিলাম ‘শপথ’ কবিতা, যেটি পরিচয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। পরিচয় নিষিদ্ধ হবার পর সংবাদ এর শারদীয়া সংখ্যায় লিখেছিলাম ‘মাংসাশীর জন্য বিজ্ঞাপন-১৯৪৮’ নামক স্যাটায়ার কবিতা
‘আসুন আসুন! কার তাজা মাংস চাই
হাতে যেন থাকে খাঁটি খদ্দরের থলি
পরম স্বাধীন মাংস নিয়ে খান ভাই
অহিংসার হাড়িকাটে দিয়েছি এ বলি।’
— শেষ দুটো চরণ ছিল—
‘ভূতপূর্ব বিপ্লবীর মাংস নিরামিষ
সর্বত্রই ব্রাঞ্চ আছে দিল্লি হেডাপিস।’
সঙ্গে সঙ্গে বেআইনি হল সংবাদ পত্রিকা। তখন মনুমেন্টের গায়ে গানের লিস্ট করে পুলিশ টাঙ্গিয়ে দিত ‘এই গানগুলি গাওয়া বেআইনি’ বলে। খুব গর্ব হতো যে তার মধ্যে অধিকাংশ গানই থাকত আমার। লাখ লাখ লোকের জমায়েত হত ময়দানে। আমরা গান গাইতে এলে পার্টি কর্মীরা কর্ডন করে আমাদের ঘিরে রাখতেন। গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে দিতেন আমাদের। পুলিশ খুঁজে পেত না। সে একটা যুগ গেছে, যেন একটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে দিয়ে দিনরাত্রিগুলো কেটে যেত— মাথায় খালি নতুন নতুন গানের ভাবনা। পকেটে রুমালে বাঁধা ভিজে ছোলার র্যাশন নিয়ে দিনের পর দিন অর্ধাহারে অনাহারে কেটে যেত, গায়েই লাগতো না। ‘বিপ্লব’ ওই দিগন্তের ওপারেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। আরো কিছু সংগ্রাম আরো কিছু আত্মত্যাগ করলেই তার প্লাবন এসে অত্যাচার অনাচারকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে মুক্তির সূর্যের দারোদ্ঘাটন করে দেবে এমনিই ছিল আমাদের বিশ্বাস আর প্রত্যয়। তিন তিনটে ওয়ারেন্ট মাথায় নিয়ে কখনো কৃষকের ঘরের মাচায়, কখনো রেলের খালি ওয়াগনে, কখনো বা নৌকার পাটাতনে লুকিয়ে হেঁটে হেঁটে বাদা ভেঙে ভেঙে চাষির পল্লীতে পৌঁছে মিটিং হত। ক্লান্তি শ্রান্তি বলে কোন জিনিস ছিল না। আজ ভাবি কি করে এসব সম্ভব হয়েছিল! কি এক অপূর্ব উন্মাদনায় সত্যি মনে হোত ‘জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য’।
ক্রমে দক্ষিণ কলকাতা গণনাট্য সংঘের সংগীত শাখা গড়ে উঠল আমার নেতৃত্বে— সুগায়িকা গীতা মুখার্জ্জীর গরচার বাড়িতে বসত আমাদের রিহার্শাল। অভিজিৎ ব্যানার্জ্জী, প্রবীর মজুমদার, অনল চট্টোপাধ্যায় (এরা তিনজনেই পরে সংগীত পরিচালক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন) সুগায়ক হীরালাল সরখেল, প্রখ্যাত কমেডিয়ান পিয়ানোবাদক রনজিৎ রায়ের মেয়ে ছবি রায় ইত্যাদিকে নিয়ে গানের দল গড়ে উঠল। এখানেই রচিত হল— ‘পথে এবার নামো সাথী’— ‘ধিতাং ধিতাং বোলে’। কোরাস গানের পদ্ধতি নিয়ে এখানে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে থাকে ‘আলোর পথ যাত্রী’ ‘মানবোনা বন্ধনে’ – ‘ও মোদের দেশবাসীরে’– ‘আমার প্রতিবাদের ভাষা’ ‘ঢেউ উঠছে কারা টুটছে’ ইত্যাদি গান হার্মনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমরা গাইতাম। পার্টির মিটিং ছাড়া আমাদের ডাক পড়তো বিভিন্ন কলেজের ছাত্র সম্মেলনে, ক্লাবের জলসায় এবং কলকাতার বাইরে বিভিন্ন মফঃস্বল অঞ্চলের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে। আমাদের গানের দলের খ্যাতি ক্রমশ উঠল তুঙ্গে। আমরা অনুষ্ঠান শেষ করার পর তাবড় তাবড় শিল্পীরা আসর জমাতে ভয় পেতেন। একবার আমার মনে আছে যাদবপুরে একটি অনুষ্ঠানে আমরা ছাড়া বহু নামকরা শিল্পীরাও এসেছেন। তার মধ্যে ছিলেন স্বনামধন্য পঙ্কজ মল্লিক। ওঁর গান স্বভাবতই শেষে, রাখা হয়েছিল, তার আগেই ছিল আমাদের গান। আমাকে ডেকে পঙ্কজদা বললেন ‘সলিল, আমি আগে গেয়ে নিই তার পরে তোমরা গেও কেমন? তোমাদের ওই সব হৈচৈ গানের পর. . . ইত্যাদি. . . আমি বললাম: ‘অবশ্যই। আপনি আগে গান।’
১৯৪১ থেকে ১৯৫১ এই দশ বছরে নানা উত্থান পতন ঝড়ঝঞ্ঝাটের মধ্যে দিয়ে বহু গান রচিত হয়েছে, আজ তা ইতিহাস। গণনাট্য শুধু নয়। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র সব আন্দোলনের শরিক হতে পেরে আমার সংগীত জীবনে পরিপ্রেক্ষিত নির্ধারিত হয়েছে। সুরে নতুন মূর্ছনা যোগ হয়েছে। মার্কসবাদী চেতনা মানসিকতার নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। সমষ্টি থেকে ব্যক্তি জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার কথাও যখন গানে এসেছে, একটা সুপ্ত চেতনা কাজ করেছে তার বিষয়বস্তুর এবং আঙ্গিকের নির্ধারণে। আজও সেই চেতনা জীবনের প্রতি মুহূর্তে ভালোমন্দ বুঝতে শেখায়, ভয়কে জয় করতে শেখায়। কুসংস্কার, ধর্মান্ধতাকে যুক্তিবাদের শাণিত অস্ত্র দিয়ে খণ্ডন করতে শেখায়। যে-উৎসভূমি থেকে গণসংগীতের ধারা নেমে এসেছিল। সেই একই উৎসভূমি থেকে উদ্গত জীবন দর্পণ আমাদের হতাশায় আলো জ্বেলে দেয়, মানবজাতির উজ্জল ভবিষ্যৎ যে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে আসতে বাধ্য সেই আশাবাদ এবং প্রত্যয় জীবন সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। তাই বেঁচে থাকা সার্থক হয়।